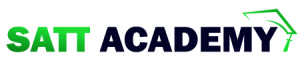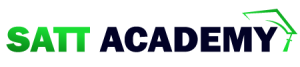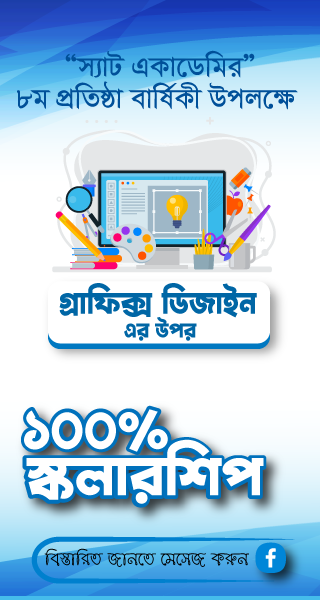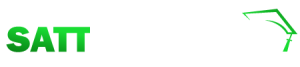খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস সমকোণী ত্রিভুজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেন। সমকোণী ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্য পিথাগোরাসের বৈশিষ্ট্য বলে পরিচিত। বলা হয় পিথাগোরাসের জন্মের আগে মিসরীয় ও ব্যবিলনীয় যুগেও সমকোণী ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার ছিল। এ অধ্যায়ে আমরা সমকোণী ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলো বিশেষ নামে পরিচিত। সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভুজ এবং সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় যথাক্রমে ভূমি ও উন্নতি। বর্তমান অধ্যায়ে এ তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।
অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-
➤ পিথাগোরাসের উপপাদ্য যাচাই ও প্রমাণ করতে পারবে।
➤ ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে ত্রিভুজটি সমকোণী কি না যাচাই করতে পারবে।
➤ পিথাগোরাসের সূত্র ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
চিত্রে, ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ, এর ∠ACB কোণটি সমকোণ। সুতরাং AB ত্রিভুজটির অতিভুজ। চিত্রে ত্রিভুজটির বাহুগুলো a, b, c দ্বারা নির্দেশ করি।
কাজ : ১। একটি সমকোণ আঁক এবং এর বাহু দুইটির উপর যথাক্রমে 3 সে.মি. ও 4 সে.মি. দূরত্বে দুইটি বিন্দু চিহ্নিত কর। বিন্দু দুইটি যোগ করে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁক। ত্রিভুজটির অতিভুজের দৈর্ঘ্য পরিমাপ কর। দৈর্ঘ্য 5 সে.মি. হয়েছে কি? |
লক্ষ কর, 32 + 42 52 অর্থাৎ দুই বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের বর্গের যোগফল অতিভুজের পরিমাপের বর্গের সমান।
সুতরাং a,b,c বাহু দ্বারা নির্দেশিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রে c2 = a2 + b2 হবে। এটা পিথাগোরাসের উপপাদ্যের মূল প্রতিপাদ্য। এই উপপাদ্যটি বিভিন্নভাবে প্রমাণ করা হয়েছে । এখানে কয়েকটি সহজ প্রমাণ দেওয়া হলো।
আমরা জানি সংস্কৃতি স্থির বিষয় নয়। পরিবর্তন সংস্কৃতির ধর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে ভিন্নতা থাকলেও সেখানে প্রতিনিয়ত সংযোজন ও বিয়োজন চলে। একসময় সংস্কৃতির পার্থক্য বা পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আবার নতুন সংস্কৃতির পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে। সংস্কৃতির এই পরিবর্তনশীলতার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন:
সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি : সাধারণত দুইটি সমাজের সংস্কৃতি একে অপরের সংস্পর্শে এসে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এই কাছে আসা যত বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে সংস্কৃতির আদান-প্রদান তত বেশি হবে। এর মাধ্যমে একে অপরের সংস্কৃতির কিছু না কিছু গ্রহণ করবে। সংস্কৃতির এই চলমান গতিধারা এবং এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে সংস্কৃতির প্রসার লাভকে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বলে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রসার বা ব্যাপ্তি ঘটে। বিশ্বায়নের ফলে এবং প্রযুক্তির উন্নতিতে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে গেছে।
সাংস্কৃতায়ন : নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে অন্য কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানকে নিজ সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়াকে সাংস্কৃতায়ন বলা হয়। আমাদের দেশ বহুবার বহিরাগত শাসক দ্বারা শাসিত হওয়ায় এখানে সাংস্কৃতায়ন প্রবল। ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শই সাংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার কারণ বলে মনে করা হয়। যেমন : ইংরেজরা প্রায় দুইশ বছর আমাদের শাসক ছিলো বলে অনেক ইংরেজি শব্দ আমাদের ভাষায় মিশে গেছে।
সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ : আত্তীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অন্যের সংস্কৃতি আয়ত্ত করে। যেমন: মানুষ যখন কোনো নতুন সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাস করতে আসে তখন সেখানকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ এক কথায় সমগ্র জীবনধারার সাথে আত্তীকৃত হতে চেষ্টা করে। এভাবে একসময় তা আত্তীকরণ হয়ে যায়। যেমন: জীবিকার প্রয়োজনে, বৈবাহিক কারণে অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিজ এলাকা থেকে স্থানান্তর হলে মানুষ ঐ এলাকার সংস্কৃতির সাথে নিজেকে আত্তীকরণ করার চেষ্টা করে।
সাংস্কৃতিক আদর্শ : প্রতিটি দেশ বা সমাজের রয়েছে নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক আদর্শ। সাংস্কৃতিক আদর্শ বলতে কোনো দেশ বা সমাজের মানুষের সংস্কৃতির ধরনকে বোঝায়। এগুলো হলো- আচার- আচরণ, খাদ্য, পোশাক, বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, লোককাহিনি, সংগীত, লোককলা ইত্যাদি। কোনো দেশ বা সমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শের মাঝে ঐ দেশ বা সমাজের মানুষের জীবনপ্রণালি ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। এই আদর্শের কারণে সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় ।
প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন : আধুনিক প্রযুক্তি বা বস্তুগত সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সমাজে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে গোটা বিশ্ব এখন একটি বিশ্বপল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনেক উন্নত হয়েছে। এখন ঘরে বসে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের খবর জানা যায়। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে। অনুন্নত সংস্কৃতি দ্রুত উন্নত সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ করছে। এভাবে প্রযুক্তি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।
একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান।
(দুইটি সমকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে)
বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC সমকোণী ত্রিভুজের ∠B = 90°
অঙ্কন : BC কে D পর্যন্ত বর্ধিত করি, যেন CD = AB = c হয়।
D বিন্দুতে বর্ধিত BC এর উপর DE লম্ব আঁকি, যেন DE = BC = a হয়। C, E ও A, E যোগ করি।
প্ৰমাণ :
| ধাপ | যথার্থতা |
|---|---|
(১) ∠ABC ও ACDE এ AB = CD = c, BC = DE = a এবং অন্তর্ভুক্ত ∠ABC = অন্তর্ভুক্ত ∠CDE সুতরাং, ∆ABC ≅ ∆CDE ∴ AC = CE = b এবং ∠BAC = ∠ECD (২) আবার, AB ⊥ BD এবং ED ⊥ BD বলে AB || ED সুতরাং, ABDE একটি ট্রাপিজিয়াম। (৩) তদুপরি, ∠ACB + ∠BAC = ∠ACB + ∠ECD = এক সমকোণ। ∴ ∠ACE = এক সমকোণ। ∴ ∆ACE সমকোণী ত্রিভুজ। এখন ABDE ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ( ∆ ক্ষেত্র ABC + ∆ ক্ষেত্র CDE + ∆ ক্ষেত্র ACE) বা, বা, বা, (a + c) (a + c) = 2ac + b2 [2 দ্বারা গুণ করে] বা, a2 + 2ac + c2 = 2ac + b2 ∴ b2 = c2 + a2 (প্রমাণিত) | [প্রত্যেকে সমকোণ]
[বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য]
∴ ∠BAC = ∠ECD
[ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল x সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব]
|
পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিকল্প প্রমাণ
(সদৃশকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে)
বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC সমকোণী ত্রিভুজের ZC = 90° এবং অতিভুজ AB = C, BC = a, AC = b প্রমাণ করতে হবে যে, AB2 = AC2 + BC2
অর্থাৎ c2 = a2 + b2
অঙ্কন : C বিন্দু থেকে অতিভুজ AB এর উপর লম্ব CH অঙ্কন করি। AB অতিভুজ H বিন্দুতে d ও e অংশে বিভক্ত হলো।
প্ৰমাণ :
| ধাপ | যথার্থতা |
|---|---|
∆ВСН ও ∆АВС এ ∠BHC = ∠ACB এবং ∠CBH = ∠ABC (১) ∴ ∆CBH ও ∆ABC সদৃশ। ∴ ∴ … …(1) (২) অনুরূপভাবে ∆ACH ও ∆ABC সদৃশ৷ ∴ … … (2) (৩) অনুপাত দুইটি থেকে পাই, a2 = c × e, b2 = c × d অতএব, a2 + b2 = c × e + c × d = c (e + d) = c × e = c2 ∴ c 2 = a2 + b2 [প্রমাণিত] | প্রত্যেকেই সমকোণ সাধারণ কোণ
[(i) উভয় ত্রিভুজ সমকোণী (ii) ZA কোণ সাধারণ]
∵ c = e + d |
পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিকল্প প্রমাণ
(বীজগণিতের সাহায্যে)
পিথাগোরাসের উপপাদ্য বীজগণিতের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায়।
বিশেষ নির্বচন : মনে করি, একটি সমকোণী ত্রিভুজের
অতিভুজ c এবং a, b যথাক্রমে অন্য দুই বাহু।
প্রমাণ করতে হবে, c2 = a2 + b2
অঙ্কন : প্রদত্ত ত্রিভুজটির সমান করে চারটি ত্রিভুজ চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে আঁকি।
প্ৰমাণ :
| ধাপ | যথার্থতা |
|---|---|
(১) অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রটি বর্গক্ষেত্র। এর ক্ষেত্রফল (a + b)2 (২) ছোট চতুৰ্ভুজ ক্ষেত্রটি বর্গক্ষেত্র। এর ক্ষেত্রফল c2 (৩) অঙ্কনানুসারে, বড় বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল চারটি ত্রিভুজক্ষেত্র ও ছোট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান। অর্থাৎ, বা, a2 + 2ab + b2 = 2ab+c2 ∴ c2 = a2 + b2 (প্রমাণিত) | [বাহুগুলোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য a+b এবং কোণগুলো সমকোণ]
[বাহুগুলোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য c]
|
| কাজ : ১। (a–b)2 এর বিস্তৃতির সাহায্যে পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি প্রমাণ কর। |
বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের জীবন আচরণ বা সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। একে বলা হয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এছাড়া ধর্মীয় সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির প্রভাবও একেবারে কম নয়; যেমন : পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, সংগীত, কলা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, ফ্যাশন ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যাকে আমাদের সংস্কৃতি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয় । বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে তো বটেই শহরের জীবনেও ইদানীং বিভিন্ন লোক উৎসব, বর্ষবরণ, মেলা ইত্যাদির আধিক্য ও বিভিন্ন লোক সামগ্রীর সম্ভার দেখে এই পরিবর্তন স্পষ্টই চোখে পড়ে। বিশ্বায়নের প্রভাবেও বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। আগে যেমন যাত্রা, পালাগান, সার্কাস, জারিসারির মাধ্যমে মানুষ বিনোদনের চাহিদা পূরণ করত, বর্তমানে ঘরে বসে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সে চাহিদা পূরণ করছে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে ।
বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় সংস্কৃতিতে আমাদের দেশে পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এক্ষেত্রে বস্তুগত সংস্কৃতি এগিয়ে আছে। যত দ্রুত আমরা ফ্রিজ, টেলিভিশন গ্রহণ করি তত দ্রুত অন্য দেশের ধ্যান- ধারণা, দৃষ্টিভংগি ও বিলাস সামগ্রী গ্রহণ করতে পারি না। বাংলাদেশে পারিবারিক ব্যবস্থায় বা পারিবারিক সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, পূর্বের যৌথ পরিবার ভেঙে এখন একক পরিবার গ্রাম শহর উভয় স্থানে গড়ে উঠেছে। যা তাদের আচার-আচরণে ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে প্রকাশ পাচ্ছে ।
অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ফলে পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর সমঅধিকার ও নারী স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নারী-পুরুষের চিরায়ত সম্পর্কে পরিবর্তন এনেছে। এখন নারী-পুরুষ একত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে।
প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আমাদের সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে । এই পরিবর্তন মানুষের জীবন যাপন, পেশা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডিজিটাল নির্ভরতা বাড়িয়ে দিয়েছে । যার ফলে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হচ্ছে ।
কাজ : সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দাও ।
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের ইতিবাচক বা ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এছাড়া শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, গবেষণা, খেলাধুলা, বিনোদন, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, বৈদেশিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, নারী- পুরুষ সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটেছে।
কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ও শিক্ষায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতিতে উন্নয়ন বয়ে আনছে ।
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণে আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, বহুজাতিক কোম্পানি, আধুনিক বিপণী বিতান ইত্যাদির সম্প্রসারণ হয়েছে। ফলে এগুলোকে ঘিরে এক ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে যা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করছে।
বিশ্বের উন্নত দেশের অনুকরণে প্রচলিত ধারার শিক্ষার সাথে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা চলছে। আবার প্রচলিত ধারার শিক্ষার পাশাপাশি দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এসব পরিবর্তন মূলত শিক্ষা সংস্কৃতিরই পরিবর্তন, যা শিক্ষার সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে।
বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম বা প্রাইভেট চ্যানেল প্রতিষ্ঠার ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়েছে। যার মাধ্যমে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটছে দ্রুত এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাদের আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটছে। এটি একটি সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।
কাজ : মাটির প্লেট থেকে চিনামাটির প্লেটের ব্যবহারকে কী বলা যায়?
যদি কোনো ত্রিভুজের একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান হয়, তবে শেষোক্ত বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণটি সমকোণ হবে।
বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ∆ABC এর AB2 = AC2 + BC2 প্রমাণ করতে হবে যে, ∠C = এক সমকোণ।
অঙ্কন : এমন একটি ত্রিভুজ DEF আঁকি, যেন ∠F এক সমকোণ, EF = BC এবং DF = AC হয়।
প্ৰমাণ :
| ধাপ | যথার্থতা |
|---|---|
(১) DE2 = EF2 + DF2 = BC2 + AC2 = AB2 ∴ DE = AB এখন ∆ABC ও DEF এ BC = EF, AC = DF এবং AB = DE. ∴ ∆ABC = ∆DEF ∴ ∠C = ∠F ∴ ∠C = এক সমকোণ। [প্রমাণিত] | [কারণ ∆DEF এ ∠F এক সমকোণ] [কল্পনা]
[বাহু-বাহু-বাহু সর্বসমতা] [∵ ∠F এক সমকোণ] |
বাঙালি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী একটি প্রাচীন জাতি । মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, যেসব জিনিস ব্যবহার করে, যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, যা কিছু সৃষ্টি করে, সব নিয়েই তার সংস্কৃতি। খাদ্য, বাসস্থান, তৈজসপত্র, যানবাহন, পোশাক, অলঙ্কার, উৎসব, গীতবাদ্য, ভাষা-সাহিত্য সবই তার সংস্কৃতির অংশ। তবুও এর মধ্যে সৃষ্টিশীল কিছু কিছু কাজ সংস্কৃতির বিচারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোকে আমরা বলি শিল্পকলা। আমরা আমাদের সেই সব সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হব এবং দৃশ্যশিল্প, সাহিত্যশিল্প ও সঙ্গীতশিল্প এই তিন শাখায় আমাদের অবদান ও কীর্তি স্মরণ করব।
দৃশ্যশিল্প : এগুলো বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিত। পলিমাটিতে গড়া আমাদের এই দেশ। এই দেশে একদিকে মাটি আর অন্যদিকে এ মাটিতে জন্মানো বাঁশ মানুষের ঘর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনির্মিত ঘর হলো মাটির তৈরি ও বাঁশের তরজার ছাউনিযুক্ত দোচালা, চারচালা, এমনকি আটচালা। কখনো কখনো বাঁশের কাঠামোর উপর শন দিয়ে চাল ছাওয়া হয়েছে। এখনও গ্রামগঞ্জে এরকম ঘর দেখা যায় ।
একসময় ছাঁচ অনুযায়ী মাটির তৈরি ইট দিয়ে মন্দির বানানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শিল্পমূল্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি অঙ্কন করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এগুলোকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। দিনাজপুরের কান্তজি মন্দিরে এভাবে পোড়ামাটির শিল্পকর্মে রামায়ণের কাহিনিসহ নানা সামাজিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারেও পোড়ামাটির প্রচুর কাজ আছে। এতে সেকালের সমাজ জীবনের ছবি পাওয়া যায়। কালো রঙের কষ্টিপাথর আর নানা রকম মাটি দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বানানোর ঐতিহ্যও বেশ পুরনো।
তবে পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙ দিয়ে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে তার প্রশংসা আধুনিক বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। হাজার বছর পরেও ছবিগুলো চমৎকার ঝকঝকে রয়েছে। পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের।
বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। প্রাচীন বাংলার দুকূল কাপড়ের বেশ খ্যাতি ছিল। কৌটিল্য বলেছেন, পুণ্ড্রদেশের (উত্তরবঙ্গ) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ। দুকূল ছিল খুব মিহি আর ক্ষৌমবস্ত্র একটু মোটা। পত্রোর্ণ নামে এন্ডি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো মগধ ও পুণ্ড্রে। সেকালে এদেশের দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো ।
বাংলায় বিভিন্ন সময় যেসব কাপড় উৎপন্ন হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উতানি, সুসিজ, কোসা, মলমল, দুরিয়া, শিরবান্দ ইত্যাদি। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের ছিল যে এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনি বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার শাড়ির খ্যাতিও বহুকালের- সিল্ক, জামদানি, টাঙ্গাইল, মসলিন, গরদ ইত্যাদি এখনও সুপরিচিত।
সুলতানি আমল থেকে বাংলার স্থাপত্যশিল্পে ইরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে। গম্বুজ ও খিলানসহ মসজিদ তো নির্মিত হয়েছেই, অনেক দপ্তর ও বাড়িঘরও তৈরি হয়েছে এই রীতিতে। ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটরা, ঢাকার লালবাগের কুঠি এ সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন।
বাংলার নকশিকাঁথার কথা না বললেই নয়। গ্রামীণ নারীরা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনি ও ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখনও গ্রামীণ সমাজের নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন।
এছাড়া কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শঙ্খের কাজ, বাঁশ-বেত ও শোলার কাজেও বাংলার মানুষ যেমন দক্ষতা দেখিয়েছে তেমনি তাদের সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটিয়েছে।
কাজ- ১ : বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে এমন কয়েকটি দৃশ্যশিল্পের উল্লেখ করো।
কাজ- ২ : পোড়ামাটির কাজ বলতে কী বুঝায়? কয়েকটি কাজের দৃষ্টান্ত দাও।
কাজ-৩ : বাংলার প্রাচীন দৃশ্যশিল্পের তালিকা তৈরি করো। এসবের নিদর্শন ও ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করো।
সাহিত্য : বাঙালির প্রথম যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় তা চর্যাপদ নামে পরিচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন। পরে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন। তিনি গবেষণা করে জানান প্রায় বারোশো বছর আগে বৌদ্ধ সাধকরা এগুলো লিখেছেন। এখন হয়ত আমাদের পক্ষে এগুলো বোঝা কঠিন হবে। তাছাড়া শাব্দিক অর্থ ছাড়াও এগুলোর ভাবার্থও বুঝতে হয়। এগুলোই হলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুইপা এবং কাহ্নপা প্রমুখ। আমরা নিচে চর্যাপদের একটি নমুনা ও তার অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হব।
লুই পা লিখেছেন-
কা আ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল
বাংলায় এর শাব্দিক অর্থ হলো-
শ্রেষ্ঠ তরু এই শরীর, পাঁচটি তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল (ধ্বংসের প্রতীক) প্রবেশ করে। এর ভাবার্থ হলো— শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডাল স্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে জানাশোনা চলে। এতে বেশি আকৃষ্ট হলে বস্তুজগতকেই মানুষ চরম ও পরম জ্ঞান করে ক্ষতির সম্মুখীন হয় ।
সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে । শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনি নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিতি। বৈষ্ণব সমাজব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমানে এতই ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল যে অনেক মুসলমান কবিও পদাবলি রচনা করেছেন।
দেশীয় দেবদেবীকে নিয়েও নানা কাব্যকাহিনি রচিত হয়েছে এক সময়। এগুলো মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সেকালের বাংলার সমাজচিত্র পাওয়া যায়৷
মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনি এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম। আলাওল রচিত পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত ৷
ইংরেজ আমলে উনিশ শতকে আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যার উপর সৌধ তুলেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন।
কাজ- ১ : বাংলার সাহিত্য বিকাশের একটি ধারাবাহিক চিত্র দাও।
কাজ- ২ : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কয়েকটি নিদর্শনের পরিচয় দাও।
সংগীত শিল্প
বাংলা চিরকালই সংগীতের দেশ। এখানকার মাঠে-প্রান্তরে কৃষক হাল চাষ করতে করতে যেমন গান বেঁধেছে তেমনি নদী ও খালে নৌকা বাইতে বাইতে মাঝিও গলা ছেড়ে গান গেয়েছে। আবার সাধারণ মানুষ তার মতো করে গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছে। আমরা সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় আমাদের দুই আদি সংগীত চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলীর কথা আগেই জেনেছি । কীর্তনগান প্রধানত হিন্দু সমাজে হতো, এখনও হয়। তবে বাউল ও ভাটিয়ালি গান গ্রামের হিন্দু- মুসলমান সকলেই গেয়ে থাকে। মুর্শিদি, পালাগান, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি বহু ধরনের আঞ্চলিক লোকগান ছড়িয়ে আছে সারা বাংলা জুড়ে ।
শহরাঞ্চলে একসময় পাঁচালি, খেউড়, খেমটা প্রভৃতি গানের আসর বসত। তবে উত্তর ভারতের সংস্পর্শে এসে হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে বাঙালি সংগীত সাধকদের পরিচয় ঘটে। তার প্রভাবে এখানে নাগরিক সংগীতের বিকাশ ঘটে। নিধুবাবু, কালী মির্জা প্রমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায়। তাঁরই গান আজ আমাদের জাতীয় সংগীত— ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এ গানের সুর তিনি নিয়েছেন বাউল গানের সুর থেকে। রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে পরে আরও অনেকেই বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আপন স্বাতন্ত্র্যে ও বৈচিত্র্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। মাত্র কুড়ি বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি প্রায় ছয় হাজারের মতো গান লিখেছেন। অতুল প্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন আধুনিক বাংলা গানের সমৃদ্ধিতে এদের অবদানও ব্যাপক।
কাজ : বাঙালির সংগীত সম্ভারের পরিচয় দাও।